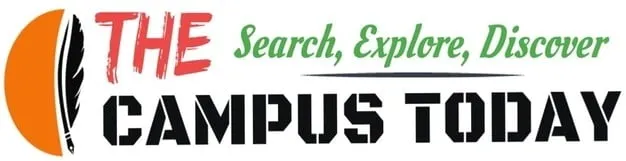একুশের করুণ বিদায়

এমএ জাহাঙ্গীর
একুশ এলেই ভাষার গানে মুখরিত হয় সারা বাংলাদেশ। যা মূলত পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায়। আবেগ আর আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা মর্যাদা হারিয়েছে বৈকি। একুশ শব্দটিই এক সময় শোকের তরবারি, ইস্পাতের তৈরি দুধারি তলোয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে এখন সেটা সোনার দরবারি তরবারি বনে গিয়েছে।
যা দরবারে ঝুলিয়ে রাখা যায়, তবে ব্যবহার করা যায় না। এখন শোক মাত্র একটি উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। বায়ান্নর আন্দোলনের বিশ্বজনীনতা ঘটেছে ঠিক। বিশ্বায়নের গুণে বাংলা ভাষারও বিশ্ব-বিস্তৃতিও ঘটেছে। তবে যা হয় নি তা হলো প্রকৃত ব্যবহার। দেশে এবং বিদেশে কোথাও নয়।
আর ভাষার ইতিহাস? একবিংশ শতাব্দীতে কতজন ইতিহাসের সেই নায়কদের মনে রেখেছে সেটা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। সম্প্রতি দেখা গেছে যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ একটি একুশের ব্যানারে ছবি ছাপিয়েছে ৭১ এ শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের। অবশ্য এটিকে অনেকে সাধারণ ভুল বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে পরপরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগও একই কাজ করেছে। তখন আলোচনায় এসেছে বিষয়টি।
বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবুল কাশেম বলেছেন যে, বিজ্ঞান অনুষদের এরকম ভুল গ্রহণযোগ্য হলেও কলা অনুষদের এই ধরনের ভুল ক্ষমার অযোগ্য। অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট বুঝাতে চেয়েছেন যে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা চেতনার একুশ ভুলে যেতেই পারে।
অধ্যাপক আবুল কাশেমের কথা অনুযায়ী এসব ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পরপরই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একটি ব্যানারেও দেখা যায় যে একুশের ব্যানারে বীরশ্রেষ্ঠদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ইতিহাস বিষয়টি যাদের পাঠ্য তারাই ভুলে গেলেন ভাষা শহীদদের। ভুলটি শিক্ষার্থীদের উপর দিয়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে বেশ। বিপত্তি ঘটে যখন ইতিহাস বিভাগের সভাপতি নিজেই বললেন যে, ভাষা শহীদদের তিনি চেনেন না। এতসব কাণ্ডকাহিনীর পর কিভাবে বুঝতে পারি যে সত্যই ভাষা দিবস এবং ভাষা শহীদদের আমরা ধারণ করছি?
যাকগে এসব ভুলের কথা বা ভুলে যাওয়ার কথা কিংবা অবহেলার কথা। ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিহাস যতটুকু সাক্ষ্য দেয় তাতে স্পষ্ট যে, সরকারি কর্মসহ বিভিন্ন মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার চাই। চাই সরকারি-বেসরকারি সব কাজকর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার। এ দাবি আদায়ের জন্য বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ সেই পাকিস্তান আমলে সর্বত্র, বিশেষ করে ঢাকা শহরে দোকানপাটে ইংরেজি সাইনবোর্ড, নিওন সাইন ভেঙেছে। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা, সরকারি ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য বাংলা একাডেমি বহু কাজকর্ম করেছে। শব্দকোষ, অভিধান প্রকাশ করেছে। নানা গবেষণা চালাচ্ছে, চলছেও।
ভাষা আন্দোলনের মূল কথা ছিলো, জাতীয় জীবনে মুখের ভাষা ও মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা দান। অন্য ভাষার উচ্ছেদ নয়, স্বাধীনতার পর নিজের ভাষাকে ব্যবহারোপযোগী করার আগেই ইংরেজির মতো সমৃদ্ধ ভাষাকে তাড়াতে গিয়ে আমরা উন্নত বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জানালা বন্ধ করে ফেলি এবং একঘরে হয়ে পড়ি। সম্প্রতি শুনেছি যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরও সংখ্যা বেড়েছে অধিক। পাল্লা দিয়ে বের হচ্ছে বাংলা বইপত্র, সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যবহার ও মর্যাদা কি সঠিকভাবে বেড়েছে?
একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষিত বাঙালির মুখে ইংরেজি ও বাংলা মিশ্রিত একটি অদ্ভুত ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। যার নাম দেয়া হয়েছে বাংরেজি। এর প্রাধান্য প্রকটভাবে বিস্তৃত হয়েছে সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে, এমনকি সাংবাদিকতায়ও।
প্রশ্ন করলেই সরাসরি উত্তর আসে যে এটা নাকি আধুনিকতা। তবে ইদানীংকালে বাংরেজির পাশাপাশি বাংলাবান্দিরও উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ, বাংলা এবং হিন্দি মিলেই এটি গঠিত। আধুনিকতার ফলে অনেকেই ছোট করে বান্দি ভাষাও বলে থাকেন এটিকে। যা গণমাধ্যমের সহযোগে তরুণ সমাজের শিকড়ে পর্যন্ত পেঁৗছে গেছে ইতোমধ্যে। মূলত বাংলাদেশে হিন্দি টিভি সিরিয়ালের ব্যাপক প্রচলনে জনজীবনের একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত ভাষায় চলনে, বলনে, কথনে তার ব্যাপক কুপ্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভাষা দিবস বা বাংলা নববর্ষ দিবস ছাড়া শাড়ি পরিহিতা নারী ঢাকা শহরেও দেখা যায় খুব কম।
শাড়ি পড়েও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উপায় বের হয়েছে বেশিদিন হয় নি। শাড়ির মধ্যে বাংলা বর্ণ লেখা থাকে। এই বিষয়টি সুন্দরভাবে নেওয়া যায়। অনেকে বিদ্রুপও করে থাকেন হয়তো। তবে বিদ্রুপ করার মতো মনে হয় না কখনোই। অন্তত ভাষাটা শরীরে ধারণ করলেও তো ভালো। তবে সেই শাড়িতে যখন বাংলা বর্ণের পাশাপাশি হিন্দি বর্ণ লেখা থাকতে দেখা যায় তখন সেটিকে সত্যিই বিদ্রুপ না করে উপায় নেই। এবারের বইমেলায় এমনটিই দেখা গেছে। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে নজর কেড়েছে কিছু মানুষের।
সকল ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বিরুদ্ধাচরণ করতে রাজি নই। কারণ ভালো দিকও থাকতে পারে এসবের। তবে কষ্ট পাই যখন দেখি ভাষা ও সংস্কৃতি আধিপত্যবাদী রূপ নিয়েছে। ভাষার আধিপত্যবাদ একটি ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র, স্বাধীনতা ও বিকাশের জন্য বিরাট বাধা হয়ে দঁাড়াতে যথেষ্ট নয় কি? পাকিস্তান আমলে বাঙালির সংগ্রাম উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে ছিল না। ছিল উর্দু ভাষার আধিপত্যবাদী ও ঔপনিবেশিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। বাঙালিরা তো এটাই চেয়েছিলেন যে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির উপর যেন উর্দু চাপিয়ে না দেওয়া হয়। বিজয় লাভের পর স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও তার হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি কি আবার বান্দি বা বাংরেজির আধিপত্যবাদী গ্রাসে অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে না?
স্বাধীন বাংলাদেশে হয়তো বান্দি বা বাংরেজির সরাসরি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে তথ্যযুগের নবপ্রযুক্তির বিস্ময়কর বিস্তারের বদৌলতে বাংলাদেশে সবার অলক্ষ্যে কুমিরের পুঁটিমাছ ভক্ষণের মতো হিন্দি ভাষা ও কালচারের বাংলা ভাষা কালচারকে গ্রাসের নিঃশব্দ আয়োজন চলছে। তা হওয়ার কথাও বটে। কারণ আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আমরা ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা থেকে পিছিয়ে পড়ার পর আবার এমনভাবে ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরি যে, বাংলা ভাষা নামেমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে থেকে যায়, শুরু হয় সরকারি কাজকর্মে, বহু ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যেও একটি অনুন্নত ইংরেজি ভাষার ব্যবহার। বাংলা ভাষার সাহায্যে উন্নত বিশ্বে বর্তমানের প্রবল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও তো কঠিন। বাঙালির প্রচুর মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এ ভাষা বিভ্রাটে তারা উন্নত বিশ্বে শিক্ষা অর্জনে, কর্মসংস্থানে গিয়ে এশিয়ার অনেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে পারে না সবসময়।
একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভাষার জন্য আবার একটি আন্দোলন বোধহয় এবার জরুরী। অন্তত উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতার নিগড় ভেঙে দেওয়া উচিত। আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসনের মুখে গণভাষারূপে সব কৃত্রিমতা বর্জন করে বাংলা ভাষার পুনর্নির্মাণ, তাকে ব্যবহারিক ভাষা করে তোলা এবং আন্তর্জাতিক উন্নত ভাষাগুলোর সমকক্ষ করে তোলার আন্দোলন। সেইসাথে প্রয়োজন ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে প্রজন্মকে জানান দেওয়া। ভাষা শহীদ এবং ভাষার আন্দোলনকে চেনানোর সময় হয়তো এখন এসেছে। এতে হয়তো ঢাকা মেট্রো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বস্তরে অন্তত ভাষা শহীদদের চিনতে পারবে।
লেখকঃ সংবাদকর্মী এবং শিক্ষার্থী,
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।